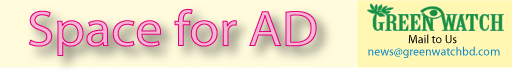- Bangladesh Bank Buys $115 Million to Support Forex Market |
- Tarique Rahman, Daughter Zaima Added to Voter List |
- NCP and LDP Join Jamaat-Led Eight-Party Alliance |
- Tarique Rahman’s gratitude to people for welcoming him on his return |
- Attorney General Md Asaduzzaman resigns to contest election |
বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস: বয়ঃসন্ধিতে এই প্রবণতার কারণ ও তা প্রতিরোধে ব্যবস্থাপনা

বিপাশা মুখার্জি যিনি পেশায় ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার একটি স্কুলের শিক্ষিকা এবং এক বয়ঃসন্ধির কিশোরীর মা, তিনি তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন ভয়েস অফ আমেরিকা-র সঙ্গে, “করোনা অতিমারির সময়ে অনলাইন ক্লাসের জন্য আমার মেয়ে প্রথম ফোন হাতে পায়। ক্লাস ও পড়া দিয়ে শুরু হলেও সামাজিক মাধ্যমে অবাধ যাতায়াত চলতে থাকে। মোবাইলের নেশা এমনি হয়ে দাঁড়ায় যে, আমরা বাবা মা হিসেবে বারণ করলেও আমাদের ভুল বুঝতে থাকে ও। সেইসময়ে অতিমারির কারণে ক্লাস টেন-এর বোর্ডের পরীক্ষা না হলেও ক্লাস টুয়েলভ-এ স্কুল খুলল এবং বোর্ডের পরীক্ষাও অফলাইনে হওয়ার কথা ঘোষণা হয়। পরীক্ষার প্রায় দশদিন আগে থেকে শুরু হয় চূড়ান্ত অস্থিরতা। দীর্ঘদিনের পড়ার ঘাটতি পূরণ করতে না পারায় শুরু হয় মানসিক চাপ ও উদ্বেগ। পরীক্ষার থেকে বাঁচার জন্য নোট লিখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া এমনকি আত্মহননের কথাও ও ভাবছিল তখন।”
এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে যোগ করা যায় আরও তিনটি বাস্তব ঘটনার কথা, যা সংবাদমাধ্যমে উঠে এসেছিল।
সদ্য বিদ্যালয়ের গণ্ডি পাশ করে দু চোখে অনেকটা উজ্জ্বল স্বপ্ন নিয়ে কলকাতার বুকে এক নামী কলেজে ভর্তি হয় এক কিশোরী। মা নেই। অতি সাধারণ চাকুরে বাবা-ই পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। সবসময়ে ঘরে ও বাইরে সমানতালে সামলে উঠতে না পারায় তিনি মেয়েকে প্রতিদিনই খাবার জন্য দিয়ে দিতেন কিছু টাকা। অন্যদিকে শহরের চাকচিক্য, বন্ধুদের সাজপোশাক, আদবকায়দা মেয়েটির মনে জাগায় চূড়ান্ত অস্থিরতা। “আমাকেও ওদের মতো ওদের ‘লেভেলে’ পৌঁছতে হবে।” শুরু হল অন্য লড়াই। প্রায় না খেয়েই টাকা জমিয়ে চলতে লাগল পোশাক, প্রসাধনী কেনার পালা। সকলের অগোচরে সব ঠিকই চলছিল কিন্তু হঠাৎ ছন্দপতন। ক্লাসে মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে যায়- একবার নয়, বার তিনচারেক। শিক্ষকরা তৎপরতার সঙ্গে বিষয়টি দেখেন। মেয়েটি প্রাথমিকভাবে কিছু না বললেও পরে জানায় আসল কারণ এবং বলে ফেলে – “আমার মনে হয় আত্মহত্যা করি। আমার জীবনে তো কিছু নেই। আমার কাছে তো জীবন মূল্যহীন।”
দশম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী। মোবাইল ফোন কেনা নিয়ে বাড়িতে প্রবল অশান্তির জেরে স্কুলের টয়লেটে গিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে।
একাদশ শ্রেণির এক শিক্ষার্থী প্রেমঘটিত কারণে স্কুলে হাতের শিরা কেটে ফেলে, এবং এও জানা যায় তার আগেও দশবার বিভিন্নভাবে সে এই চেষ্টা করেছিল।
উপরের ঘটনা তিনটি ভিন্ন জায়গার হলেও চূড়ান্ত উদ্বেগের বিষয় হল ‘আত্মহত্যার প্রবণতা’ এবং এই তিন জনই মেয়ে, যাদের বয়স ১৫-২০ র মধ্যে। সময়টি বয়ঃসন্ধি ও তা পেরিয়ে দু-এক বছর। এই সময়ে শারীরিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক পরিবর্তনও ঘটতে থাকে যার জন্য মনের মধ্যে তৈরি হয় অস্থিরতা।
রিহ্যাবিলিটেশন সাইকোলজিস্ট পাপড়ি চট্টোপাধ্যায় বলছেন, “বয়ঃসন্ধিকাল একটা এমন সময় যখন নানাবিধ চাপ তাদের মধ্যে তৈরি হতে থাকে, তাদের বোধ তৈরি হতে থাকে, কিন্তু অভিজ্ঞতা নেই, তাই বোধের সম্পূর্ণ কাঠামোগত চরিত্রটা তাদের কাছে পরিষ্কার হয় না। একটা অস্ফূট বোধ তৈরি হয় মাত্র ভেতরে। অথচ বড়রা ভাবেন – তুমি তো অনেক কিছু বুঝছো, তাহলে তুমি সেই অনুযায়ী আচরণ করছো না কেন? আবার ছোটরা ভাবে – আমরা যখন বুঝছি, তখন আমাদের সেই মর্যাদাটা দেওয়া হচ্ছে না কেন? এই চাপগুলোর জন্য নানারকম যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি মনের মধ্যে বা সামাজিকভাবে তৈরি হয়। এই বয়সে যে আত্মহত্যার হারটা বাড়া থাকে এবং আগের থেকে যে এই হার বেড়েছে, এটা সঙ্গত।” তিনি আরও জানান, আত্মহত্যা বিষণ্ণতার চরম রূপ। এই বিষণ্ণতাকে যাতে আমরা সাধারণ মন খারাপের সঙ্গে গুলিয়ে না ফেলি সেই বিষয়ে আমাদের সচেতনতা ভীষণ প্রয়োজন।
বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস
সারা বিশ্বে এই আত্মহত্যার প্রবণতা কমিয়ে সচেতনতা বাড়িয়ে তোলার উদ্দেশেই ১০ই সেপ্টেম্বর পালিত হয় ‘বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস’। এর স্লোগান হল ‘Creating hope through action’ অর্থাৎ ‘কাজের মধ্যে দিয়ে আশা তৈরি’। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা WHO-এর দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতি বছর গোটা বিশ্বে ৭ লক্ষ ৩ হাজার জন মানুষ আত্মঘাতী হন যাদের মধ্যে বেশিরভাগই ১৫-২৯ বছর বয়সী। এর বাইরেও কয়েক কোটি মানুষ রয়েছেন, যারা ভয়াবহ অবসাদের সঙ্গে লড়াই চালাতে চালাতে প্রতিনিয়ত আত্মহত্যার কথা ভেবে থাকেন। এছাড়াও ভারতের National Crime Records Bureau (NCRB)-র রিপোর্টে একটি বিশেষ তথ্য উঠে আসছে – কোভিড অতিমারির আগে ভারতে আত্মহত্যার সংখ্যা তুলনামূলক কম ছিল। কোভিডের ফলে বেড়েছে সামগ্রিক অবসাদ। NCRB সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী- ২০১৯ এ ভারতে এই সংখ্যাটি ছিল ১,৩৯,১২৩ আর ২০২১-এ তা বেড়ে দাঁড়ায় ১,৬৪,০৩৩।
আত্মহত্যার প্রবণতা ও আত্মহত্যার ঘটনা বেড়ে যাওয়ার কারণ
বয়ঃসন্ধি থেকে ২৪-২৫ বছর পর্যন্ত বয়সীদের মধ্যে বেড়ে চলা আত্মহত্যার কারণ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে উঠে আসছে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় – মানসিক চাপ, আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির চাপ, অবসাদ ও সামাজিক চাপ ও ব্যক্তিগত চাপ তৈরি হওয়া। তাছাড়া বয়ঃসন্ধির ছেলেমেয়েরা মূলত তাদের আত্মপরিচয়ের সংকটে দিশেহারা। তাদের সামনে সারাক্ষণ সামাজিক মাধ্যমে যে জীবন তুলে ধরা হচ্ছে তাতে তারা দিশেহারা। যতটা উন্মুক্ত জীবনের কথা প্রচার করা হচ্ছে বাস্তবিক সামাজিক অবস্থানের মধ্যে কোথাও সেই জীবন তারা সেভাবে পেয়ে উঠছে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা মনের কথা বলতেও অক্ষম।
মনোবিদ যা বলছেন
মনোবিদ পাপড়ি চ্যাটার্জি যে কারণগুলি তুলে ধরলেন -
- প্রথম ও প্রধান হল প্রতিযোগীতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা। এই বয়সে এসে যোগ হয় তুমি ভবিষ্যতে কোন পথ বাছবে সেই পথের প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষাটিতে তুমি পারছো কি না, নাহলে জীবন শেষ হয়ে গেল। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য থাকে বিশাল চাপ। যারা প্রতিযোগীতায় নিজেদের ঠিক আত্মস্থ করতে পারছে না, লড়াইয়ের ময়দানে নেমেও যারা নিজেদের মানসিক স্থিতাবস্থা রাখতে পারছে না, তারা আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। চাপ নিতে পারছে না। চাপকে সামলানোর মতো যে মানসিক গঠন, তা তৈরি হওয়ার অবকাশটাই সে পাচ্ছে না।
- এছাড়া এই বয়সে একটা একাকীত্ব বোধ তীব্রভাবে কাজ করে। বাবা-মাকে এই সময় ভাইটাল রোল প্লে করতে হয়। কিন্তু এই বয়সেই বাবা-মায়ের থেকে তারা সরে যেতে থাকে। অথচ বাবা-মাকেই তাদের সবচেয়ে বেশি দরকার হয়। এই বোধটা বেশির ভাগের মধ্যেই থাকে না। এই বোধটা বাবা-মায়ের মধ্যে থাকাটা জরুরি। অনেক সময়ে বাবা-মায়ের জানার মধ্যে থাকে না, সন্তান কতটা দূরে সরে গেছে, কতটা বিষণ্ণতার শিকার হচ্ছ বা সন্তান কতটা ভুল কাজ কোন দিকে করে ফেলছে বা কতটা একাকীত্ব সে সাফার করছে।
- সঙ্গী নির্বাচন এই বয়সে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ জায়গা নেয় এবং সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া, একাকীত্ববোধ থেকেই যার জন্ম। এর থেকেও অনেক সময়ে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে। অনেক ঘটনা ঘটে আত্মহত্যার অ্যাটেম্পট নিয়েছে, বিষণ্ণতায় ডুবে গেছে – আমার ফিঁয়সেকে আমার বন্ধু নিয়ে নিল, আমাকে পাত্তা দিল না। এই বিষয়গুলো বয়ঃসন্ধিতে সম্মানহানির ব্যাপার হয়, তার হেরে যাওয়ার ব্যাপার থাকে। সঙ্গী নির্বাচন, সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে না পারার কারণেও আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ে।
- এই বয়সে অহং বোধ মাথাচাড়া দেয়। তাদের মধ্যে একটা সবজান্তা মনোভাবা দেখা যায়। তারফলে একটা বিনয়ের অভাব দেখা দেয়।
শিক্ষক, অভিভাবকেরা যা বলছেন
এই প্রসঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা অর্পিতা ভট্টাচার্য বলেন – “বর্তমানের তরুণ প্রজন্মের অনেকের মধ্যেই একটা ইউটোপিয়ার জগতে বাস করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যার সঙ্গে আমাদের বাস্তব জগতের সম্পর্ক প্রায় বিচ্ছিন্ন বললেই চলে। প্রসঙ্গত, পশ্চিমবাংলায় আমরা বেশিরভাগ মানুষ যে ধরণের আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলে থাকি সেই জগতে অনেক আশা, ইচ্ছে আমাদের পূরণ করা সম্ভব হয় না। ফলত তৈরি হয় মানসিক অস্থিরতা – মানসিক চাপ। ছেলেমেয়েরা বাস্তব অবস্থানের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা থেকেই সমস্যা সমাধানে অপারগ হয়ে বেছে নিচ্ছে এই পথ।”
এই অভিমতের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত পোষণ করেছেন কলকাতার একটি স্কুলের সিনিয়র শিক্ষিকা চৈতালি ভদ্র। এর সঙ্গে তিনি সংযোজন করেছেন আরেকটি বিষয়- ‘না’ শোনার অস্থিরতার কথা। “আসলে যৌথ পরিবার থেকে বাবা-মা আর সন্তান মিলে যে একক পরিবার গড়ে ওঠে তাতে আত্মকেন্দ্রিকতার জন্ম হয়। অনেক সময়ে অভিভাবকরা না চাইতেই সন্তানদের অনেক জিনিস দিয়ে দেন এবং সেটি অভ্যাসে পরিণত হওয়ার পর ‘দেবো না’ বা ‘দিতে পারব না’ জাতীয় কথা তাদের ভীষণ ভাবে মানসিক চঞ্চলতা বাড়িয়ে তোলে। আবার অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকরাও তাদের সন্তানের মেধা বুঝে উঠতে পারেন না। একটা তুলনা চলতে থাকে অন্যের সন্তানের সঙ্গে। সন্তানকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবের মধ্যে ফারাক চলে এলেই জন্ম নেয় হতাশা যা তারা সন্তানদের ওপর চাপিয়ে দেন।“
“আজকালকার পার্টিতে কেবল মধ্য বয়স্করা একা বোধ করে না বয়ঃসন্ধিও করে। তাকে পোশাকে, শরীরের আয়তনে, উপস্থিতির মহিমায় যে টেক্কা দিতে হবে অন্য বয়ঃসন্ধিকে। সবাই একটা রঙ্গমঞ্চে উঠে পড়েছে। তুলনা, তুলনা খেলাটা চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছে গেছে। তারফলে কোথাও সে আরাম পাচ্ছে না। কী করবে সে? মূলত আত্মপরিচয়ের সংকটে দিশেহারা আজকের বয়ঃসন্ধির কিশোর-কিশোরীরা। তাদের সামনে স্কুলে থাকার সময়টুকু বাদে সারাক্ষণ ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটস অ্যাপ স্টেটাস ইত্যাদির মাধ্যমে যে জীবন তুলে ধরা হচ্ছে বাস্তবিক স্কুলের পরিবেশ, বাড়ির পরিবেশে, আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে – কোথাওই আজকের বয়ঃসন্ধি সেটা পাচ্ছে না। অভিভাবকেরা এখন নিজেদের পেশার দাবিদাওয়া নিয়ে বাস্তবিকই অতি ব্যস্ত, নিউক্লিয়ার পরিবারের কমফোর্ট জোন হয়ত অভিভাবকের জন্য ভালো কিন্তু একা বাড়িতে নিজের অসংখ্য প্রশ্ন, সমস্যা নিয়ে লড়তে থাকা বয়ঃসন্ধির পক্ষে ভালো নয়। জীবনের অসংখ্য দাবি নিয়ে একটা ভীষণ আবেগী মন তাই বেছে নিচ্ছে আত্মহত্যাকে,” – জানিয়েছেন এক বেসরকারি স্কুলের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান শাশ্বতী মজুমদার।
এই মানসিক অবসাদ প্রসঙ্গে কলকাতার এক স্কুলের সিনিয়র শিক্ষক কণিষ্ক ভট্টাচার্য মনে করেছেন- “সামাজিক মাধ্যমে আত্ম-উদযাপনের অমোঘ টানের মধ্যে মুক্তি খোঁজার ভুল পথ কমবয়সীদের আরো অন্ধকার ও একাকিত্বের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ভারত এক দীর্ঘ আর্থিক ও সামাজিক অস্থিরতার মধ্যে আছে বলে আমার মনে হয়। অতিমারির পর তার মাত্রাবৃদ্ধি হয়েছে। সরকারি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পরিসর কমছে ও সেই শিক্ষার সঙ্গে কাজের বাজারের যোগ কমে আসছে। বেসকরকারি শিক্ষার বিপুল আর্থিক ব্যয় সঙ্কুলানের চিন্তা পরিবারে অভিভাবক থেকে শিক্ষার্থী সকলের ওপর চেপে বসেছে। একদিকে ব্যাপক হারে কাজ হারিয়েছে মানুষ আরেকদিকে অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির কারণে জীবনযাত্রার মান তলানিতে ঠেকছে সাধারণ মানুষের। এর যে সামাজিক প্রভাব তা পরিবারের ছোটোদের, শিক্ষার্থীদের ওপরে প্রকাণ্ড চাপ তৈরি করছে। কোথাও পরিবারের প্রয়োজনে এদের কাজে যোগ দিতে হচ্ছে নয়ত সামাজিক পারিবারিক প্রত্যাশার চাপ বহন করতে হচ্ছে। যে বাস্তবিক সামাজিকীকরণ, মেলামেশা এই প্রকাণ্ড চাপ ভাগ করে নিতে, সহনীয় করে নিতে সাহায্য করত তার অবকাশ কমে আসছে আশঙ্কাজনক হারে।”
বয়ঃসন্ধির মেয়েদের মধ্যে কেন বাড়ছে
ভারতীয় সমাজের একটা বড়ো অংশে, এখনও মেয়েদের সমাজিক এবং পারিবারিক ক্ষেত্রে কখনও রক্ষণশীল মানসিকতা, কখনও স্টিরিওটাইপ-এর কারণে নানা বৈষম্যের মুখোমুখি হতে হয় যার প্রভাব ব্যক্তি জীবনে ভয়ানকভাবে পড়ে।
মনোবিদ পাপড়ি চ্যাটার্জির মতে, “মেয়েরা ছেলেদের থেকে একটু ইন্ট্রোভার্ট হয়, অন্তর্মুখী। মেয়েদের আমরা চট করে বাড়ির বাইরে সেইভাবে মিশতে দেখি না। ছেলেদের আমরা যেভাবে আমাদের সমাজে ছাড়ি...হয়তো এখন হচ্ছে, আগের থেকে বেড়েছে...কিন্তু মেয়েদের কোথাও একটা রাশ টানা থাকে। আবার মেয়েদের হরমোনাল বা শারীরিক কারণেও মেয়েরা কোথাও ‘উইকার সেক্স’ হিসাবে সামাজিকভাবে পরিচিত হওয়ার কারণে অনেক সময়ে বহু মেয়েই অতিরিক্ত হীনমন্যতায় ভোগে। এটা হাজার পড়াশোনা শেখার পরেও থাকে অনেকের। সামাজিক চেতনার অভাব তো রয়েইছে – যতই তুমি পড়াশোনা করো, তুমি কিন্তু মেয়ে এটা মনে রাখবে। এই আপ্তবাক্য তাদের সামনে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। মেয়েদের জন্য লড়াইয়ে তাই আমরা অনেক সময়েই বলি, মেয়েরা লড়াই অনেক পেছন থেকে শুরু করে। এইসব কিছুর জন্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে মেয়েদের লড়াকু মনোভাবও কোথাও টাল খেয়ে যেতে পারে। বয়ঃসন্ধির মেয়েদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বা ঘটনা তাই বেশি।”
“ভারতীয় সমাজের একটা বড়ো অংশে, এখনও মেয়েদের সমাজে পরিবারে একেবারে মূলগত মানসিকতার কারণে নানা অসাম্যের মুখোমুখি হতে হয়। এমনকি সেটা বাড়িতে খাবারের পরিমাণের থেকে গৃহশ্রমের ক্ষেত্রেও। সামাজিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব আরো ব্যাপক। কেবল শিক্ষক বা অভিভাবকের সংবেদনশীলতায় এর কিছুটা লাঘব করা গেলেও, উপরিকাঠামোর মূলগত পরিবর্তন না হলে তা পূর্ণত ফলপ্রসূ হবে না বলেই মনে হয়,” মত কণিষ্ক ভট্টাচার্যর।
বিপাশা মুখার্জি জানান, “আমার মেয়ে সাজগোজ বা ‘বাইরের লুক’ নিয়ে কোনদিনই সেভাবে ভাবত না। কিন্তু ক্লাস নাইন থেকে চারপাশের বন্ধুদের এই বিষয়ের মাত্রাতিরিক্ত সচেতনতা ওকে চিন্তিত করে। যেহেতু ও নিজে তেমন ভাবে সাজতে পারে না ফলত বন্ধুদের ‘বুলি’-র শিকার হতো। সেখান থেকে জন্ম নেয় হীনমন্যতা। মনে ইচ্ছে থাকলেও এই ‘তুলনার খেলা’য় মেতে অন্যদের সবসময়ে টেক্কা দিতে না পারায় ওর মনে জন্মাচ্ছে অশান্তি।”
শাশ্বতী মজুমদার যেমন বলেন- “এটা আসলে সভ্যতার সেই সংকট বেলা যখন চোখের সামনে আমরা সমস্যাটা দেখেও কাল ভেবে দেখব আজ থাক বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঢুকে ঘুমের বড়ি জোগাড় করছি। আর পাশের ঘরে কিংবা ঠিক আমার আপনার পাশে শুয়ে থাকা বয়ঃসন্ধি হাতরে হাতরে খুঁজে যাচ্ছে "I Quite" এর বড়ি।”
সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধের উপায়
শিক্ষকরা যা বলছেন
আত্মহত্যার আগে তাই আসে আত্মহত্যার ঝুঁকি। এক্ষেত্রে চৈতালি ভদ্র মনে করেন, শিক্ষক হিসেবে আগে বোঝাতে হবে এটা একটা ক্রাইম। নিজের জীবনকে শেষ করার কোন অধিকার নেই মানুষের। যার জন্য এখনও স্বেচ্ছা মৃত্যুর অধিকার নিয়েও লড়াই চলছে। প্রত্যহ পড়ার মধ্যে দিয়েই জীবনের পাঠও দেওয়া প্রয়োজন – শেখাতে হবে ধৈর্য এবং আত্মনির্ভরতার শিক্ষা। মানুষের দুই ধরণের পরিচয়ের কথা তিনি বলেন- জন্মগত ও অর্জিত। দ্বিতীয় পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার জন্য তাদের উৎসাহ দিতে হবে। ব্যক্তিগত ও অর্থনৈতিক উভয় স্বাধীনতাকে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে অর্জন করতে হবে।
এই প্রসঙ্গে অর্পিতা ভট্টাচার্য জানান – ‘University Grants Commission (UGC)-র নির্দেশে বিগত চার বছর ধরে মেন্টরিং সেশনকে লাগু করা হয়েছে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে। UGC গাইডলাইন দিয়েছে কীভাবে এবং কেমন ধরণের আলোচনা করা যেতে পারে। সেখানে কিন্তু এই আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে আটকানোর কথাও বলা হয়েছে। এই সেশনে বিভাগীয় মেন্টরের সঙ্গে আন্তরবিভাগীও মেন্টরও থাকেন। যাতে শিক্ষার্থীরা মন খুলে কথা বলতে পারে। আমাদের যেহেতু গার্লস কলেজ ফলে শিক্ষার্থীদের থেকে এই উদ্যোগের বিপুল সাড়া পাই আমরা। এই ধরণের সেশন তারা আরও চায়। এটা একটা ইতিবাচক দিক।”
মনোবিদের পরামর্শ
মনোবিদ পাপড়ি চ্যাটার্জি আত্মহত্যার প্রবণতা প্রতিরোধে যে পরামর্শগুলি দিলেন:
- সাধারণ বিষণ্ণতাকে সাধারণ অবস্থাতেই আমাদের বুঝে নিতে হবে। পরিবারের বড়দের – বাবা, মা, দাদা-দিদি, শিক্ষ-শিক্ষিকা সকলকেই নজর দিতে হবে, বয়ঃসন্ধির ছেলে বা মেয়েটির আচরণে কোনও পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে কি না। নোটিস করতে হবে, গায়ে না পড়ে খতিয়ে দেখতে হবে – কী হয়েছে। এই বয়সের ছেলেমেয়েরা একটু সহানুভূতি পেলে নিজেদের মেলে ধরতে পারে। কোথাও তাদের বোঝার অভাব হলেই তারা বিষণ্ণতা বোধে আক্রান্ত হয়, নিজের থেকে বলতে না পেরে। কিছু ছেলে, মেয়ে তো ইন্ট্রোভার্ট হয়ই। এই অন্তর্মুখী স্বভাবের জন্য, নিজের চিন্তাভাবনা প্রকাশ করতে না পারার জন্য বাড়িতে তাদের পিছিয়ে পড়া বলে ট্রিট করা হয়। এরাই গুরুত্ব পেলে, ধৈর্য ধরে তাদের সঙ্গে অনেকটা সময় ধরে কথা বললে, নিজেদের মেলে ধরতে পারে, নিজের ভাবনা প্রকাশ করতে পারে।
- কখনও বয়ঃসন্ধিকালের ছেলে, মেয়েদের নেতিবাচক কথা বলব না। মানে, তাদের পারফর্ম্যান্স, তাদের এবিলিটি, তাদের ব্যবহার সম্পর্কে – তোমার এরচেয়ে ভালো হবে না, তোমার জন্য লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে, তুমি কিছুই পারো না – এধরনের কথা একেবারেই বলা যায় না, এরা ভীষণ সেনসেটিভ হয়।
- এই বয়সে কমিউনিকেশন প্রব্লেম তৈরি হয়, অভিমানে অনেক কথা বলতে পারে না। নেতিবাচক কথা বললে, তারাই আরও পিছিয়ে যায়, যত পিছিয়ে যায়, তত হীনমন্যতাবোধে আক্রান্ত হয়, তত বিষণ্ণতা চেপে ধরে। তাই ধৈর্য ধরে তাদের বুঝতে হবে, বোঝাতে হবে।
- এই বয়সের ছেলে, মেয়েদের বুঝতে দিলে চলবে না, রাশটা অভিভাবকের হাতেই রয়েছে। খুব পোলায়েটলি, কাম অ্যান্ড কোয়াএটলি তাদের ডিল করতে হবে, দেখতে হবে বিষণ্ণতাটা যেন তাদের চেপে না ধরে। এবং তাদের হেরে যাওয়া শেখাতে হবে।
- মেয়েদের সঙ্গে কখনওই ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বৈষম্যমূলক কথাবার্তা বলা যাবে না। অনেকে বলেন, “আমার মেয়েকে, আমার ছেলের মতোই মানুষ করছি”, কিন্তু যখন বাড়িতে যখন মেয়েটি বড় আর ছেলে ছোট, তখন কোনও কাজ সেই দিদিটির শরীর খারাপ থাকলেও ভাইটিকে করতে শেখানো হয় না। বা বোনকে কোনও কাজে সাহায্য করতে দাদাকে শেখানো হয় না। সব সময়েই আচরণে বুঝিয়ে দেওয়া হয় মেয়ে আর ছেলের মধ্যে কোথাও একটা পার্থক্য আছে। এটা কাম্য নয়। ওরা ভীষণ সেনসেটিভ, আগের থেকে অনেক সচেতন, এটা এই বয়সে খুবই সমস্যা তৈরি করে, আজীবন ছাপ রেখে দেয়।
- শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বলা হচ্ছে না যে, বকবেন না। কিন্তু মনে রাখতে হবে শাসন হবে বয়সোচিত। ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যে শাসন, বয়ঃসন্ধিকালে তা চলবে না। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে যথোচিত, সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখেও বয়ঃসন্ধির ছাত্রছাত্রীদের সুন্দরভাবে ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব। তথ্য সূত্র ভয়েস অফ আমেরিকা বাংলা।