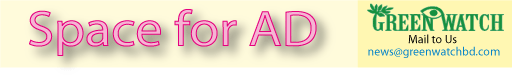- NCP Vows to Contest All 300 Seats in Upcoming Polls |
- Trump's Tariff Hike: How will it affect Bangladesh? |
- Myanmar: UN chief for urgent access as quake toll mounts |
- AI’s $4.8 tn future: UN warns of widening digital divide |
- Volker Turk warns of increasing risk of atrocity crimes in Gaza |
ঢাকাকে তিস্তা সংরক্ষণে সহায়তা করার প্রস্তাব কি অর্থবহ পদক্ষেপের দিকে নিয়ে যাবে?

People in the Bangladesh part of the Teesta Basin now face a devastating flood.
আমরা গভীর আগ্রহের সাথে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সর্বশেষ দিল্লী সফরের পর ২৪ জুন আপনার জনপ্রিয় SANDRP (দক্ষিণ এশিয়া নেটওয়ার্ক অন ড্যামস, রিভারস অ্যান্ড পিপল) ব্লগে প্রকাশিত প্রতিবেদনটি পড়েছি। তিস্তা সংরক্ষণে বাংলাদেশকে সাহায্য করার জন্য ভারত একটি কারিগরি কমিটি পাঠাবে। প্রতিবেদনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঘোষণায় আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে গঙ্গা চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর জন্য আরেকটি কারিগরি কমিটিও গঠন করা হবে। এই চুক্তির মেয়াদ ২০২৬ সালে শেষ হবে। আপনাদের প্রতিবেদনে গভীর আশাবাদ ব্যক্ত করে বলা হয়েছে যে ভারত যেন কল্যানকর দৃষ্টিকোন থেকে বিষয়গুলোকে দেখে এবং সমাধান করে।
তবে দুটি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন।
উপরে বর্ণিত প্রস্তাবটি ডিপ ফ্রিজ পর্যায়ে রয়ে গেছে কারণ তিস্তা ও গঙ্গার উপর কারিগরি কমিটির গঠন এমনকী দুই দেশের মধ্যকার কার্যত সুপ্ত যৌথ নদী কমিশনকে উপেক্ষা করার একটি পদক্ষেপ। এই কমিশন অতীতে বৈঠক, নোট ও মতামত বিনিময় করেছে অভিন্ন নদীগুলোর সমস্যা সমাধানের জন্য। উভয় দেশের মধ্যে অভিন্ন নদীর সংখ্যা ৫৪টি। প্রস্তাবে তিস্তার প্রবাহ ভাগ করে নেওয়ার বিষয়েও কোন উল্লেখ করা হয়নি। অথচ ২০১১ সালে এই নদীর পানি বন্টনের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা ছিল।
তিস্তার পানি বণ্টন বা এর জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টিকে একপাশে রেখে, প্রস্তাবিত কারিগরি কমিটি – তথা ভারতীয় পক্ষ – তিস্তার বাংলাদেশ অংশে একটি জলাধার নির্মাণ দরকার হবে কিনা তা নির্ধারণের দায়িত্ব নিজেই নেবে। এর সবই এসেছে তিস্তার বর্ষায় বন্যা এবং শুষ্ক মৌসুমে নদীর পানির অভাব মোকাবেলায় এক বিলিয়ন ডলারের একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য চীনের প্রস্তাবে ভারতের অনুভূত নিরাপত্তা হুমকি বা ভূ-রাজনৈতিক বিবেচনা থেকে। বাস্তবতা হলো, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের গজল ডোবা ব্যারেজ থেকে শুষ্ক মওসুমে নদীর সম্পূর্ণ প্রবাহ সরিয়ে নেওয়া হয়। আর বর্ষায় খরস্রোতা পাহাড়ী এই নদীর বন্যার সব পানি বাংলাদেশে ছেড়ে দেয়া হয়। তিস্তার বাংলাদেশ অংশে প্রতিবছর দেখা দেয় ভয়াবহ বন্যা ও নদী ভাংগন।
অন্ততপক্ষে বাংলাদেশের তিস্তা অববাহিকার মানুষের শুষ্ক মৌসুমের দুর্ভোগ কিছুটা হলেও লাঘব করা যেত যদি ভারত এই পার্বত্য নদীর ন্যায্য অংশ দিয়ে দিত। তিস্তা বর্ষাকালে নিয়মিত ধংসাত্মক হয়ে ওঠে। সাম্প্রতিক আলোচনার সময় বা যৌথ বিবৃতিতে কোথাও এটি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি যদিও উভয় পক্ষই জানে যে এটি পুরো তিস্তা প্রশ্নের মূল বিবেচ্চ বিষয়।
তারপরে আবার তিস্তার ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের প্রশ্ন শুধুমাত্র বাংলাদেশের অভ্যন্তরেই। এটি একটি আন্তঃসীমান্ত নদীর ব্যবস্থাপনার নীতির পরিপন্থী। তিস্তা হিমালয় থেকে উতপত্তি হয়ে সিকিম ও পশ্চিম বংগ দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদীর মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। অথচ যে কারিগরি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে তাকে কেবল বাংলাদেশের মধ্যেই কাজ করার জন্য কার্য পরিধি দেয়া হচ্ছে।
একারণে যে কেউ বলতে পারেন যে এর পরিধি খুবই সীমিত - প্রস্তাবিত তিস্তা প্রকল্পে চীনের সম্পৃক্ততার আশংকা দূর করার জন্য। অথচ প্রকল্পটি প্রনীত হয়েছে বাংলাদেশে শুকনো কালে পরিবেশগতভাবে বিপর্যয়কর প্রবাহের অভাব এবং বর্ষা মৌসুমে ধংসাত্মক বন্যার প্রতিকূল প্রভাবকে মোকাবেলা করার জন্য। বাংলাদেশের মতামত বা অংশগ্রহন ছাড়াই সীমান্তের ওপার থেকে নদীর সারা বছরের প্রবাহ বৃত্তাকারে নিয়ন্ত্রিত হয়।
বলাই বাহুল্য, বাংলাদেশে তিস্তার ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের উপর উল্লিখিত কারিগরি কমিটির সংকীর্ণ ফোকাসের কারণে ভাটিতে প্রতিবেশী বাংলাদেশের কোনো উপকারী উদ্দেশ্য পূরণ করার সুযোগ খুব কম। বাংলাদেশ সময়ের সাথে সাথে তিস্তার পানির অংশের উপর তার কথা বলার অধিকার হারাতে বসেছে। প্রস্তাবিত কমিটি এখন সিদ্ধান্ত নেবে যে নদীর প্রবাহের ওপর বৃহৎ প্রতিবেশী ভারতের একতরফা নিয়ন্ত্রণ থেকে নিম্ন অববাহিকার জনগণকে রক্ষা করতে বাংলাদেশের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন আছে কি না।
বিগত দুই দশকের অভিজ্ঞতা দেখায় যে ঢাকার পরিবেশ, জীবজগত, অর্থনীতি, জীবন ও জীবিকা নির্বিশেষে ক্ষতিকর প্রভাব যাই হোকনা কেন, নদীর কোনো শুষ্ক ঋতুর প্রবাহ পাওয়া যাবে না তা নিশ্চিত। আরেকটি বিষয় যার সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট নিশ্চয়তা রয়েছে। আর তা হল যখনই সিকিমের উপরে অস্বাভাবিকভাবে ভারী বৃষ্টিপাত বা হিমবাহের বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটবে তখনই খরস্রোতা পাহাড়ি নদীর সৃষ্ট বন্যা সাথে সাথে অববাহিকার বাংলাদেশের অংশে চলে আসবে।
গঙ্গা সম্পর্কেও একটি কারিগরি কমিটি ৩০-বছরের চুক্তির নবায়নের জন্য কাজ করবে। বর্তমান চুক্তির মেয়াদ ২০২৬ সালে শেষ হবে। তিন দশক ধরে আন্তঃসীমান্ত নদীর জল বণ্টনের জ্ঞান এবং উপলব্ধির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। উভয় পক্ষই এখন যথেষ্ট ভালোভাবে বুঝতে পেরেছে যে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ বাড়ানোর অর্থ সামান্যই হবে যদি বাংলাদেশে ফারাক্কা পয়েন্টে পানি আসার কোনো গ্যারান্টি না থাকে বন্টনের জন্য, অনন্ত ভবিষ্যত বা আরও ৩০ বছরের জন্য। চুক্তির বিগত ২৮ বছরে গঙ্গার পানি চুক্তির শর্তানুযায়ী বাংলাদেশে পাওয়া যায়নি। ১৯৯৬ সালে চুক্তি স্বাক্ষরের পর প্রথম বছরেই বাংলাদেশে পানির প্রবাহ কমে দাঁড়ায় ৬,০০০ কিউসেক। চুক্তিতে তখন ৩০,০০০ কিউসেক পানি প্রাপ্তির কথা ছিল।
গঙ্গা চুক্তিতে, দুই বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিবেশীর সুবিধার জন্য, হিমালয়ে নদীর উৎপত্তি থেকে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত প্রবাহিত পানির তথ্য এবং উপাত্যের উপর ব্যাপকভাবে আলোচনা করা উচিত। ঢাকার ফারাক্কা ব্যারাজের উজানে নদীর পানির উচ্চতা বাড়া-কমা বুঝতে পারা উচিত। শুধু ন্যায্য অংশ বুঝে পেতেই নয়, বন্যা দুর্যোগের নির্ভরযোগ্য পূর্বাভাস দিতেও। কারণ গংগার বন্যা কখনও কখনও বিপর্যয়কর হয়ে ওঠে।
গঙ্গার উপর একটি নতুন চুক্তি ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট (আইডব্লিউআরএম) এর আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নীতির উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত যা হবে টেকসই। এবং সমস্ত যৌথ-অববাহিকাস্থ দেশের মানুষের সবার জন্য একটি লাভজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে। এখানে যে কেউ কল্যান কামনাকে অবশ্যই স্বাগত জানাবে কিন্তু যৌথ-নদীর এবং নিম্ন অববাহিকার অধিকারকে বাদ দিয়ে নয়। একটি নতুন চুক্তিতে পানি প্রাপ্যতার গ্যারান্টি এবং মতপার্থক্য দূর করার জন্য মধ্যস্ততার ব্যবস্থা থাকা উচিত। ভারতের সাথে উচ্চ অববাহিকার নেপালের মহাকালী পানি-বণ্টন এবং নিম্ন অববাহিকার পাকিস্তানের সিন্ধুর পানি-বন্টন চুক্তিগুলোতে এই অপরিহার্য ধারাগুলো আছে। বাংলাদেশের সাথে করা চুক্তিতেও এই ধারাগুলো থাকা অপরিহার্য।
SANDRP রিপোর্টে উল্লিখিত আরেকটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ - উদ্যোগ নেওয়ার আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরামর্শের অভাব। পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপত্তির অজুহাতে গত ১৪ বছরে কোনো তিস্তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি। এখন তার সঙ্গে পরামর্শ না করেই বাংলাদেশকে আশ্বাস দেওয়ার বিরুদ্ধে ভারতের কেন্দ্রে তিনি চিঠি দিয়েছেন। যদি তিনি উপরে উল্লিখিত পদক্ষেপের বিরোধিতায় দৃঢ় থাকেন, তাহলে কিছুই ঘটবে বলে মনে হয় না। বাংলাদেশে আমাদের প্রশ্ন, দিল্লি কি এটা জানত না?