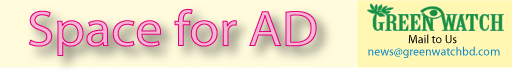- World leaders meet in Brazil to tackle global warming |
- Brazil Launches Fund to Protect Forests and Fight Climate Change |
- UN Warns Conflicts Are Devastating Ecosystems Worldwide |
- Flood-hit Kurigram char residents see little hope in politics, elections |
- Air quality of Dhaka continues to be ‘unhealthy’ Friday morning |
শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন: বাংলাদেশের শিল্পচর্চার বাতিঘর

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, যার নাম শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে ১৯৪৩-র দুর্ভিক্ষের ছবি- রাস্তার পাশে পড়ে থাকা কঙ্কালসার মানুষ, ডাস্টবিন, কাক। আরো মনে পড়ে যায় রেখাচিত্রে আঁকা গরু, গরুর গাড়ি, গ্রীবা উঁচু করে হেঁটে যাওয়া সাঁওতাল রমনীদের কথা। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন জীবনের ২৯ বছর বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি নিজেই ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। ঢাকা আর্ট কলেজ, ময়মনসিংহ জয়নুল সংগ্রহশালা, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের সূচনা তার হাত ধরেই হয়েছে। তার প্রতিটি কাজে স্বদেশী ঐতিহ্যের সাথে তিনি এশিয়া এবং ইউরোপের শিল্পের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। বাংলাদেশের চারু ও ব্যবহারিক কারুকলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তাকে গণ্য করা হয়।
ভয়েস অফ আমেরিকা-র সঙ্গে কথা বলেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের সাবেক অধ্যাপক রফিকুন নবী। তিনি জয়নুল আবেদিন সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করে বলেন, “শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন আমার শিক্ষক ছিলেন। তিনি আমাদের এই দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তার ছাত্র হতে পেরে আমি খুব গর্বিত।”
বাংলাদেশে শিল্পচর্চার প্রতিষ্ঠাতা
জয়নুল আবেদিন ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলার কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলে পড়েন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্টসের ড্রইং অ্যান্ড পেইন্টিং বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। দেশভাগের পর তিনি ঢাকায় চলে আসেন। দেশে ফিরে ১৯৪৮ সালে জয়নুল আবেদিন চিত্রশিল্পী আনোয়ারুল হক, কামরুল হাসান, খাজা শফিক আহমেদ, সফিউদ্দীন আহমেদ এবং হাবিবুর রহমানকে নিয়ে জনসন রোডের একটি বিল্ডিং-এ শুরু করেন সরকারি আর্ট ইন্সটিটিউট। শুরুতে অধ্যক্ষ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সহ শিক্ষক ছিলেন ছয় জন। মাত্র দুটি বিভাগ নিয়ে আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা পায়। ড্রয়িং এন্ড পেইন্টিং এবং কমার্শিয়াল আর্ট, যেটাকে আমরা এখন গ্রাফিক ডিজাইন বলি। মোট ছাত্র ছিলেন আঠারো জন। ১৯৫১ সালে এই আর্ট ইন্সটিটিউট সেগুনবাগিচার একটি বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৫৬ সালে আর্ট ইন্সটিটিউটটি শাহবাগে পাকিস্তান সরকারের দেয়া স্থানে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে এটি একটি প্রথম শ্রেণির সরকারি কলেজ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং এর নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের অভ্যূদয়ের পর একই প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ‘বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়’। ১৯৮৩ সালে এই প্রতিষ্ঠানটিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামোর অধীনে এনে ‘চারুকলা ইনস্টিটিউট’ নামকরণ করা হয়। অধুনা এটি অনুষদের মর্যাদা লাভ করে ‘চারুকলা অনুষদ’ নামে পরিচিত হয়েছে। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
ঢাকায় জয়নুল আবেদিনের আর্ট ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা প্রসঙ্গে রফিকুন নবী বলেন, “তিনি ১৯৪৮ সালে দেশভাগের সময় যখন দেশে চলে এলেন, এসে আর্ট কলেজ তৈরি করলেন। এটা শুধু যে নিজেদের চাকরীর সুবিধার জন্য, তা নয়। এ অঞ্চলে চারুকলা ইনস্টিটিউটের প্রয়োজন ছিলো। তখন পশ্চিম পাকিস্তানে লাহোরে অনেক পুরোনো ন্যাশনাল আর্ট কলেজ ছিলো। কিন্তু ঢাকায় কোনো আর্ট কলেজ ছিলো না। শিল্পকলা নিয়ে পড়াশোনা করতে হলে আমাদের এখানকার ছাত্রছাত্রীদের কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বে, দিল্লী যেতে হতো। সেকারণেই তিনি অন্যান্য সহযোগী শিল্পীদের নিয়ে এই ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। এদেশে ঢাকা এবং চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে শিল্পচর্চার ক্ষেত্র তৈরি করছেন তিনি।”
ভয়েস অফ আমেরিকা-র সঙ্গে আরো কথা বলেছেন চিত্রশিল্পী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের সাবেক অধ্যাপক মামুন কায়সার। তিনি বলেন, “শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সে সময় আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বলেই আজকে সেখান থেকে অনেক শিল্পী তৈরি হয়েছেন। যার যার ক্ষেত্র থেকে বাংলাদেশের চিত্রকলাকে সমৃদ্ধ করেছেন। আবেদিন স্যার না থাকলে আমরা যারা শিল্পী আছি, আমাদের কারোরই জন্ম হতো না। তিনি যদি শিল্পচর্চার একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি না করতেন আমরা কেউই আজকে এ জায়গায় আসতে পারতাম না।” আর্ট ইনস্টিটিউট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “আবেদিন স্যার চিন্তা করেছিলেন, আমি যদি একা আবেদিন হই অর্থাৎ আঁকিয়ে হই তাতে বাংলাদেশের কী লাভ হবে। আমার মতো আরো অনেক আঁকিয়ের যদি সৃষ্টি হয় সেটাই বাংলাদেশের জন্য সম্মানের হবে। সেই চিন্তা থেকে তিনি আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার কথা ভাবেন।”
একজন নিবেদিত শিক্ষক
ভয়েস অফ আমেরিকা-র সাথে আলাপকালে জয়নুল আবেদিন সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেন মামুন কায়সার। তিনি বলেন, “ব্যক্তিগতভাবে স্যারের সামান্য সান্নিধ্য পাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে। আমি ১৯৭৩ সালে আর্ট কলেজে ভর্তি হই। ততদিনে স্যার আর্ট কলেজের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। তখন আমরা চিন্তা করলাম, আবেদিন স্যারকে আমরা আমাদের ক্লাসে নিয়ে আসবো। স্যার ছাত্রীদের খুব স্নেহ করতেন। বড় ক্লাসের আপুরা আর আমাদের ক্লাসমেট মেয়েরা স্যারের শান্তিনগরের বাসায় গিয়ে তাকে রাজি করায়। উনি রাজি হলেন। বলেছিলেন, আমি শুধুমাত্র ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাসে যাবো। স্যার এলেন, আমরা তাকে অপার বিষ্ময়ে দেখলাম। কালো ফ্রেমের চশমা, ব্যাকব্রাশ করা চুল, পাজামা-পাঞ্জাবী পরা। দেখলেই সম্মানে, গৌরবে মাথা নুইয়ে আসে যে ইনিই আমাদের শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। উনার কথায় ময়মনসিংহের আঞ্চলিক টান ছিলো। তিনি ক্লাসে আমাদের কাজগুলো দেখে বললেন, “তোমাদের কাজ তো দেখছি, কিছু করন লাগবো?” আমরা স্যারকে গরু আঁকতে বললাম। তিনি ব্ল্যাকবোর্ডে চক দিয়ে গরু আঁকলেন। স্যারের আঁকার ধরণ ছিলো একটু অদ্ভুত। তিনি লেজ থেকে গরু আঁকা শুরু করলেন। গরুর পেছন দিকটা, ঘাড়, মাথা এঁকে চারটা পা দিয়ে দিলেন। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম তার হাতের রেখার টান, তার ড্রয়িং। এটাই তো স্যারের বৈশিষ্ট্য ছিলো, যা আমরা তার সব ছবিতে দেখি। তারপর স্যার বললেন, “আর কিছু আঁকন লাগবো?” আমরা স্যারকে অনুরোধ করলাম, স্যারের হাতের কাক আঁকা দেখতে চাই। তিনি বললেন, “তোমরা এইডাও ছাড়বানা। তাইলে একটা কাক বসায় দেই।” বলেই গরুর পিঠে একটা কাক এঁকে ফেললেন। -এই অভিজ্ঞতাটা কোনো দিন ভুলবো না। আমাদের নবীনবরণ অনুষ্ঠানেও স্যার এসেছিলেন। বলেছিলেন, ছবি আঁকতে গেলে ভালো করে, মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে। তোমার চোখ, মন, হৃদয় সব শিল্পের মধ্যে ঢেলে দাও।
মামুন কায়সার জানান, আর্ট কলেজের ছাত্র হিসেবে বরেণ্য শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীকে সরাসরি শিক্ষক হিসেবে তিনি পেয়েছিলেন। কাইয়ুম চৌধুরী ছিলেন জয়নুল আবেদিনের ছাত্র। মামুন কায়সার বলেন, “কাইয়ুম স্যার একদিন স্মৃতিচারণ করেছিলেন- আবেদিন স্যার তাকে বলেছিলেন, তুমি নৌকা ভালো আঁকো। কিন্তু বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে তোমাকে বিভিন্ন রকমের নৌকা দেখতে হবে। তাহলেই তুমি ভালো নৌকা আঁকতে পারবে। তুমি সিলেট অঞ্চলের গয়না নৌকা দেখে আসো। ওই নৌকার গলুইতে নকশা করা থাকে। কাইয়ুম স্যার সিলেট গিয়ে সেই নৌকা দেখে এলেন, নৌকার ছবি আঁকলেন। আবেদিন স্যার খুশি হলেন। আমরা কাইয়ুম স্যারের প্রায় ছবিতেই দেখে থাকি নৌকা, নৌকার গলুই বিশেষভাবে এসেছে। এভাবেই আবেদিন স্যার তার ছাত্রদের মধ্যে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটাতেন।”
চিত্রকর্ম
জয়নুল আবেদিন ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ চিত্রমালার জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। এ ছাড়াও তার বিখ্যাত শিল্পকর্মগুলোর মধ্যে নৌকা (১৯৫৭), সংগ্রাম(১৯৫৯), বীর মুক্তিযোদ্ধা(১৯৭১), ম্যাডোনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৭০ সালে তিনি গ্রামবাংলার উৎসব নিয়ে আঁকেন বিখ্যাত ৬৫ ফুট দীর্ঘ ছবি ‘নবান্ন’। তুলির টানে কালো কালিতে আঁকা স্কেচধর্মী এই স্ক্রলটি মূলত ৪ ফুট প্রশস্ত কাগজে আঁকা। কালো কালির সঙ্গে মোম ও জলরঙেরও ব্যবহার করা হয়েছিলো। ‘সোনার বাংলার শ্মশান’ হওয়ার আখ্যান ছিল ‘নবান্ন’। এর পরপরই বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় প্রচন্ড সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসের আঘাতে তিন লক্ষাধিক মানুষ প্রাণ হারান। বিধ্বস্ত হয় উপকূলীয় জনপদ। ‘মনপুরা ৭০’ শীর্ষক ৩০ ফুট দৈর্ঘ্যের আরেকটি স্ক্রলচিত্র আঁকেন তিনি। এছাড়াও তার ভিন্নধর্মী ছবির মধ্যে আমারা দেখি সাঁওতাল দম্পতি, সাঁওতাল রমণীদ্বয়, মই দেওয়া, সংগ্রাম, বিদ্রোহী, কিংবা কাদায় পড়া কাঠবোঝাই গরুর গাড়ি ঠেলার মতো চিত্রকর্ম।
শিল্পী রফিকুন নবী, জয়নুল আবেদিনের চিত্রকর্ম সম্পর্কে বলেন, “উনি যে শিল্পচর্চা করতেন তা মূল ক্ষেত্র ছিলো মানবতা। তাঁকে মানবতার শিল্পী বলা হয়। সে কারণে গত শতাব্দীতে এবং এই শতাব্দীতে আধুনিক চিত্রকলা চর্চার যে জগৎ সে সবের মধ্যে পুরোপুরি না গিয়ে তিনি আমাদের দেশ, এই অঞ্চল, এখানকার মানুষ, প্রকৃতি এসব নিয়ে কাজ করেছেন। মানুষের দুঃখ-কষ্ট, অভাব অনটন নিয়ে কাজ করেছেন। এটা প্রথম শুরু হয়েছিলো তেতাল্লিশের মন্বন্তরের সময়। সে সময় তিনি দুর্ভিক্ষের ছবি একেঁছিলেন। আমি গর্বিত যে, তার এই স্ক্রল আঁকার সময় প্রতিদিন উপস্থিত থেকে টুকটাক সহায়তা দিতে পেরেছিলাম। খুবই নিভৃতে বাড়ির লম্বা-দীর্ঘ বারান্দায় বসে উপুড় হয়ে তিনি ছবিটি এঁকেছিলেন কয়েকদিন ধরে। সেগুলো অত্যন্ত আলোচিত হয়েছিলো সারা বিশ্বে। যারা শিল্পবোদ্ধা ছিলেন, তারা তার এই কাজগুলোর প্রশংসা করেছেন।”
জয়নুলের চিত্রকর্মের বেশিরভাগই গ্রামীণ পটভূমিতে আঁকা। এ সম্পর্কেও রফিকুন নবী বলেন, “তিনি আমাদের লোকশিল্পের উপাদানগুলোকে শিল্পকলায় আরো বেশি করে যুক্ত করেছেন। পঞ্চাশের দশকে এই লোকশিল্পের উপদানগুলোকে নিয়ে তিনি নিজে শিল্পকলার একটি ধরন তৈরি করেছেন। এটি আধুনিক চিত্রকলা চর্চার ক্ষেত্রে তার উল্লেখযোগ্য একটি সংযোজন। লোকশিল্পের আদলে ছবি আঁকতে গিয়ে তিনি লোকজ মোটিফগুলি হুবহু ব্যবহার করেননি। ফর্মগুলিকে সহজ করে এক ধরনের আধুনিক রূপ এনেছিলেন। এই আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ায় আঁকা বিশেষ মাধ্যম ছিল মূলত গোয়াশ, তেলরং, টেম্পেরা। মোটা দাগের সাহসী রেখা ব্যবহার করেছেন । বিষয় বাছাইয়ে লোকশিল্পের উপদানকে প্রাধন্য দিয়েছেন। এসবের মধ্যে গুণটানা, প্রসাধন, দুই মহিলা, পাইন্যার মা, চারটি মুখ ইত্যাদি ছবি তার নিজের প্রিয় ছিল। তার শিল্পকলার রসবোধ ও নৈপুন্যে কারণেই তিনি এত খ্যাতি অর্জন করেছেন।
প্রচ্ছদ শিল্পী জয়নুল
জযনুল আবেদিন তার কর্মজীবনের প্রথম দিকে বেশ কিছু বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকেছেন। তার আঁকা প্রচ্ছদের বেশিরভাগেই লোকজ মোটিফ থাকতো। কবি জসীমউদ্দীনের রঙিলা নায়ের মাঝি, পদ্মাপার, বেদের মেয়ে, নক্সী কাঁথার মাঠ, বালুচর, আহসান হাবীবের রাত্রিশেষ, ফররুখ আহমদের সাত সাগরের মাঝি (প্রথম সংস্করণ, ১৯৪৪), আবুল মনসুর আহমদের আয়না, ফুড কনফারেন্স, শামসুদ্দীন আবুল কালামের কাশবনের কন্যা, শওকত ওসমানের বনি আদম (প্রথম প্রকাশ আজাদ ১৯৪৬), সরদার জয়েনউদ্দীনের নয়ান ঢুলী, শামসুল হুদা চৌধুরীর ময়ূখ, কল্যাণী দত্তের ছোটদের সচিত্র কৃত্তিবাস সহ আরো অনেক বইয়ের প্রচ্ছদ একেঁছেন।
বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পথিকৃৎ
বাংলাদেশের চিত্রকলাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জনক জয়নুল আবেদিন। কেবল পূর্ববঙ্গই নয়, উপমহাদেশের চিত্রকলার ইতিহাসের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে আছেন। তাকে ছাড়া চিত্রকলা অসম্পূর্ণ। তিনি তার জীবনের দীর্ঘ সময় এ দেশের শিল্প আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি শুধু শিল্পী ও শিক্ষক নন, অন্যতম শিল্পসংগঠকও ছিলেন। ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউট ছিল সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু প্রায় এক বছরের মধ্যে ঢাকা আর্ট গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করে শিল্পীদের নিজস্ব উদ্যোগ ও আয়োজনে গড়ে তুলেছিলেন একটি সহযোগী আন্দোলন। এর সভাপতি ছিলেন জয়নুল আবেদিন। চারুকলা ইনস্টিটিউট ও ঢাকা আর্ট গ্রুপ বাংলাদেশের শিল্পচর্চা তথা সাংস্কৃতিক বিকাশে অনেক বড় ভূমিকা রেখেছে। শিল্প ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে জয়নুল আবেদিনের অগ্রণী ভূমিকার উদাহরণ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী প্রতিষ্ঠায় তার উদ্যোগ, ময়মনসিংহে জয়নুল সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব ও সহযোগিতা প্রদান এবং সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা। তিনি ১৯৬৫ সালে তার বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক ও পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ড. আহমাদ হাসান দানীর আহবানে সাড়া দিয়ে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি চারুকলা বিভাগ প্রতিষ্ঠায় মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের হাতের লেখার মূল সংস্করণ অলংকরণের নেতৃত্ব দান করেন তিনি। ১৯৫৬ সালে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন তার ছাত্র হামিদুর রহমানকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের নকশা করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন।
জয়নুল আবেদিন জীবদ্দশায় প্রায় তিন হাজারের মতো ছবি এঁকেছেন। শিল্পী মামুন কায়সারের মতে, “জয়নুল আবেদিন স্যার যদি শুধুই আঁকার জগত নিয়ে থাকতেন তাহলে তিনি আরো অনেক বেশি ছবি এঁকে যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। সেই সময়টা তিনি ব্যয় করেছেন বাংলাদেশে শিল্পী এবং শিল্পচর্চার ক্ষেত্র তৈরিতে। কিন্তু যা এঁকেছেন তাই সারা পৃথিবীতে খ্যাতি অর্জন করেছে।”
শিল্পী রফিকুন নবীর বলেন, “শিল্পকলাকে বাংলাদেশের মানুষের কাছে আদরণীয় করা, মানুষের মধ্যে শিল্পকলার বোধ জাগ্রত করা, শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে মানুষের রুচির পরিবর্তনে তার অনেক বড় অবদান রয়েছে। তিনি আমাদের শিল্পকলার ক্ষেত্রটিকে সম্মানজনক একটি জায়গায় নিয়ে গেছেন।” ১৯৭৫ সালে জয়নুল আবেদিন বাংলাদেশের প্রথম তিনজন জাতীয় অধ্যাপকদের একজন হবার মর্যাদা অর্জন করেন। তার গুণমুগ্ধ ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া ‘শিল্পাচার্য’ উপাধিতে সম্মানিত হয়েছেন এবং বস্তুতই তিনি শিল্পাচার্য।