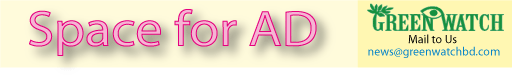- UN Debates Rsing Cvilian Toll Amid Global Conflicts |
- Lifesaving Gaza Aid Resumes After 11-Week Blockade |
- UN Reform: A Vital Process, Not a Funding Crisis Reaction |
- USAID Cuts Leave Millions at Risk of Hunger and Disease |
- UN Chief Urges Urgent Global Effort to Halt Biodiversity Loss |
বিশ্ববিদ্যালয় র্যাংকিংয়ে বাংলাদেশ তলানিতে কেন?

সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে বর্তমানে দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দেড় শতাধিক। তবে বিশ্ব কিংবা এশিয়ার র্যাংকিংয়ে মোটেও ভালো অবস্থানে নেই এসব বিশ্ববিদ্যালয়। এর কারণ কী? শিক্ষাবিদরা একেকজন এককরকম কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। কিছু পরামর্শও দিচ্ছেন তারা।
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশে ৫৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, ৩টি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১১৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে।
সম্প্রতি প্রকাশিত কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি সামগ্রিক র্যাঙ্কিংয়ে বিশ্বের সেরা ৫০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেও বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নেই। এমনকি টাইমস হায়ার এডুকেশনের এ বছরের আঞ্চলিক র্যাঙ্কিং অনুযায়ী এশিয়ার সেরা ৩০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেও নেই বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়।
সেরা ৩০০ তালিকায় ভারতের ৪০টি, পাকিস্তানের ১২টি, মালয়েশিয়ার ১১টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থান পেয়েছে। এশিয়ার ৩১ দেশের মোট ৭৩৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে র্যাংকিং করা হয়েছে।
দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে বুয়েট ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ৩০১-৩৫০ -এর মধ্যে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির অবস্থান ৩৫১-৪০০- এর মধ্যে।
জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক শাখা- ইউনেস্কোর পরামর্শ অনুযায়ী, মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৬ শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় করা উচিত। কিন্তু বাংলাদেশে ১.৭৬ শতাংশ ব্যয় করা হয়। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে শিক্ষায় বরাদ্দের হার সবচেয়ে কম। আবার যে পরিমাণ বরাদ্দ থাকে, তারও সিংহভাগ ব্যয় হয় অবকাঠামো নির্মাণ, শিক্ষক-কর্মীদের বেতন-ভাতায়। সে অর্থে গবেষণায় থাকে বরাদ্দ নামমাত্র।
কিউেএসের প্রকাশিত র্যাংকিংয়ে দেখা যায়, সেরা ১,০০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ভারতের ৪৫টি ও পাকিস্তানের ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। সেরা তিন বিশ্ববিদ্যালয় হলো এমআইটি, ক্যামব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। সেরা দশের মধ্যে এশিয়ার একটিমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় আছে। সেটি হলো ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুর।
যদিও ২০২৪ সালের কিউএস র্যাঙ্কিংয়ে সেরা ৭০০-১০০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বাংলাদেশের ৩টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়)। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৬৯১ থেকে ৭০০ অবস্থানে, বুয়েট ৮০১ থেকে ৮৫০ অবস্থানে ও নর্থ সাউথ ৮৫১ থেকে ৯০০ অবস্থানে রয়েছে।
কেন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অন্যদের চেয়ে পিছিয়ে পড়ছে- এমন প্রশ্নের জবাবে ইউজিসির সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, রেটিং প্রদান করা সংস্থাগুলো বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা সূচকে বেশি গুরুত্ব দেয়। কারণ পরিচালনায় যুক্ত থাকা ব্যক্তির কাজের প্রতিফলন দেখা যায় শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষার্থী ভর্তিতে। কিন্তু আমাদের এখানে মানদণ্ডগুলো অনুসরণ করা হয় না। নিয়োগ প্রক্রিয়াও স্বচ্ছ নয়। আর এ বিষয়গুলোর কারণে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন কঠিন হয়ে পড়ে।
শিক্ষায় পর্যাপ্ত বরাদ্দ না থাকা এবং শিক্ষকদের বর্তমান বেতন কাঠামোকেও দায়ী করেছেন এ শিক্ষাবিদ।
তিনি বলেন, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু বেসিক বিষয় আছে, যেমন পর্যাপ্ত বরাদ্দ থাকা। বাংলাদেশে তহবিল সংকট এখনও বড় সমস্যা। দেশের জিডিপির অন্তত ৬ শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় করা উচিত, সেখানে বরাদ্দ দেয়া হয় ২ শতাংশের কম। যা বিশ্ব র্যাংকিংয়ে এগিয়ে যাওয়ার অন্তরায়।
'এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বেতন বাড়ানো উচিত। সুযোগ-সুবিধা কম থাকায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক বিদেশে ডিগ্রি নিতে গিয়ে আর দেশে ফেরেন না। আর খুব কম সংখ্যক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যাপ্ত বেতন ও সুযোগ-সুবিধা দেয়। যে কারণে শিক্ষকরা গবেষণা ও প্রকাশনাতে আগ্রহী হন না', যোগ করেন তিনি।
সাধারণত একাডেমিক রেপুটেশন, এমপ্লয়ার রেপুটেশন, ফ্যাকাল্টি স্টুডেন্ট, সাইটেশনস পার ফ্যাকাল্টি, ইন্টারন্যাশনাল ফ্যাকাল্টি ও ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস, ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ নেটওয়ার্ক, এমপ্লয়মেন্ট আউটকামস ও সাস্টেইনেবিলিটিসহ বেশকিছু মানদণ্ডের বিচারে র্যাংকিং তৈরি করে রেটিং প্রদানকারী সংস্থাগুলো।
এ বিষয়ে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. অলোক কুমার পল বলেন, বিশ্ব র্যাংকিংয়ে এগিয়ে যাওয়ার শর্ত পূরণে আমাদের অনেক ঘাটতি আছে। আমরা কয়েকটি সূচকে খারাপ করছি। যেমন- আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিদেশি শিক্ষার্থীদের সব সুবিধা নিশ্চিত করতে পারে না। আমাদের এ সংক্রান্ত তহবিলের ঘাটতি আছে। এছাড়া বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে, এখানে কোনো বিদেশি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী থাকে না। ভালো রেটিং পেতে বিদেশি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর হারও গুরুত্বপূর্ণ। আর এটা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে বড় বাধা।
পাশাপাশি তত্ত্বের হালনাগাদে যথেষ্ট ঘাটতি আছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘আমাদের ইন্টাররেক্টিভ ওয়েবসাইটের অভাব রয়েছে। অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে শিক্ষকদের নাম ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। ছাত্রসহায়ক তেমন কোনো তথ্য থাকে না। কিন্তু আমাদের শিক্ষকরা যোগ্য, তাদের অনেকে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন ডিগ্রি অর্জন করেছেন। এগুলোর বিষয়ে উদ্যোগ নিলেই র্যাংকিংয়ে ভালো মান পাওয়া সহজ হয়। নিয়মিত তথ্য হালনাগাদ করে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অগ্রগতি সংস্থাগুলোকে জানানো উচিত।’
'আমাদের দেশে যেসব ডিসিপ্লিনে ছেলেমেয়েরা পড়ে, সেসব ডিসিপ্লিনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক পেশায় কাজ করার সুযোগ অনেক কম। এ কারণে খুব সহজেই শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় অনুৎসাহী হয়ে পড়ে এবং চাকরি খোঁজাই তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য যে আবহ থাকা দরকার, তা-ও নিশ্চিত করা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের যথাযথ দায়িত্ব', যোগ করেন অধ্যাপক পল।
জাতীয় পর্যায়ে একটি র্যাংকিং কাঠামো তৈরি করা প্রয়োজন বলে মনে করেন ড. অলোক কুমার পল। তার মতে, জাতীয় পর্যায়ের র্যাংকিং পেশাদারিত্বের সঙ্গে করা হলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্থান পাওয়া সহজ হবে।
কোন কোন জায়গায় উন্নতি দরকার- এমন প্রশ্নের জবাবে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত বলেন, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পরীক্ষা ও শিক্ষা পদ্ধতি বেশ ভালো, কিন্তু মূল্যায়নকারী সংস্থাগুলো তা ধরতে পারেন না। তিনি বলেন, বৈশ্বিক মানদণ্ড বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য নয়। কারণ হিসেবে তিনি ব্যাখ্যা করেন, ল্যাবের জায়গা কত বড়, ল্যাবের যন্ত্রপাতি কত, গবেষণায় কত টাকা খরচ হয়; প্রশ্নগুলো স্নাতকোত্তর বা পিএইচডি স্তরের জন্য প্রযোজ্য, কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্নাতক পর্যায় পর্যন্তই প্রাধান্য পায়।
এমআইটি বা হার্ভার্ডের সঙ্গে তুলনা না করে, সাধারণ মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তুলনা করা হোক- এ দাবি করে তিনি বলেন, ‘এমআইটি সারা বিশ্ব থেকে সেরা ছাত্র পায়, ভারতের আইআইটি সারা ভারত থেকে সেরা ছাত্র পায়। সুতরাং, আমাদের এমন প্রতিষ্ঠানের সাথে তুলনা করা উচিত যারা সারা বাংলাদেশ থেকে সেরা শিক্ষার্থী পায়। তবে আমাদের বেশির ভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের কোনো ব্যবস্থা নেই।’ সময় সংবাদ।