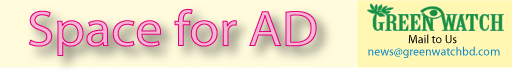- Israel Strikes Tehran with US Support Amid Nuclear Tensions |
- India Sees 9% Drop in Foreign Tourists as Bangladesh Visits Plunge |
- Dhaka Urges Restraint in Pakistan-Afghan War |
- Guterres Urges Action on Safe Migration Pact |
- OpenAI Raises $110B in Amazon-Led Funding |
দুটি উৎস থেকে বাংলাদেশে শক্তিশালী ভূমিকম্পের শঙ্কা ভূতত্ত্ববিদের
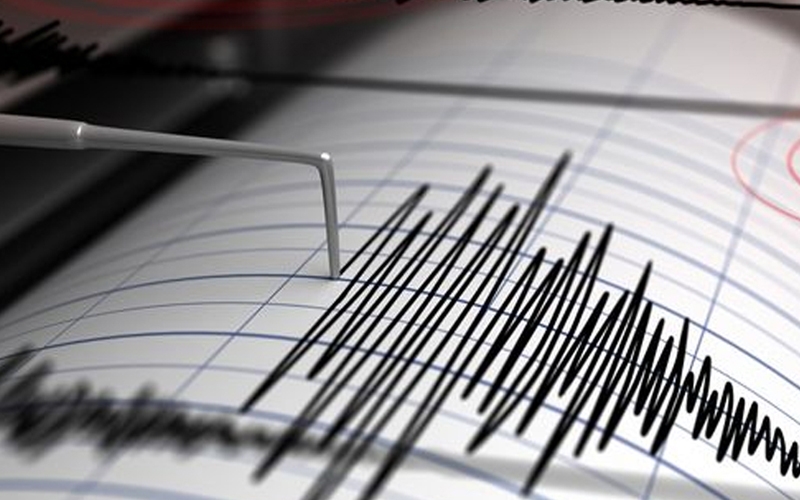
মিয়ানমারে নিমিষেই ধসে পড়ে বহুতল ভবনসহ একের পর এক স্থাপনা। ফাটল ধরে বিভিন্ন সড়কে। সেতু এবং বিমানবন্দরও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেশটিতে এখন পর্যন্ত ১,৬৪৪ জনের মৃত্যু খবর পাওয়া গেছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে আহতের সংখ্যাও।
কম্পনের প্রভাবে থাইল্যান্ডেও একটি ৩৩-তলা ভবন ধসে পড়ে, যেখানে এখনও বহু মানুষ আটকে আছে। দেশটিতে ১০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। আর আহত রয়েছেন শতাধিক। গত শুক্রবার (২৮ মার্চ) ৭.৭ ও ৬.৪ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে দুদফা কেঁপে ওঠে বাংলাদেশও।
ফায়ার সার্ভিস বলছে, মিয়ানমার-থাইল্যান্ডের মতো শক্তিশালী ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে আছে বাংলাদেশও। উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে চার অঞ্চল- ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট ও চট্টগ্রাম।
দুবছর আগে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) গবেষণায় বলা হয়, মুহূর্তেই ধসে পড়বে রাজধানীর অন্তত ৮ লাখ ৬৪ হাজার ভবন, যা মোট ভবনের ৪০ শতাংশ।
এদিকে মিয়ানমার-থাইল্যান্ডে আঘাত হানার পর বাংলাদেশের ঝুঁকি আরও বেড়েছে বলে মনে করেন ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার।
তিনি বলেন, বাংলাদেশে ভূমিকম্পের উৎস দুটি। একটি বাংলাদেশের ইন্দো-বাংলা সাবডাকশন জোন, অন্যটি ডাউকি চ্যুতি। সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ সাবডাকশন জোন। এখানেই একসঙ্গে দুটি প্লেট আটকে রয়েছে। যেখানে সঞ্চিত আছে ৮ দশমিক ২ থেকে ৯ মাত্রার শক্তি।
এই অধ্যাপক আরও বলেন, ‘একটা প্লেটের নিচে আরেকটা প্লেট। একটা ভারতীয় প্লেট আরেকটা মিয়ানমারের প্লেট। একটা প্লেটের নিচে আরেকটা প্লেট তলিয়ে যাওয়াকে বলা হয় সাবডাকশন। দুটি প্লেটের যে গতি এর ওপর নির্ভর করে কি পরিমাণ শক্তি সঞ্চিত হয়ে আছে এবং সে শক্তিটা কখন ভূপৃষ্ঠে বের হয়ে আসতে পারে।’
ভূমিকম্পের আগাম পূর্বাভাস না থাকায় ক্ষয়ক্ষতি কমাতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নেয়ার পরামর্শ এই বিশেষজ্ঞের।
তিনি বলেন, ‘ভূমিকম্পের আগে আমাদের ব্যক্তি, পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কী ধরনের প্রস্তুতি থাকা দরকার, ভূমিকম্প হলে দু-এক কদমের ভেতরে আমাদের কীভাবে নিরাপদে নিয়ে যাব এবং ভূমিকম্পের পরে কী দায়িত্ব সেগুলো জানতে হবে।’