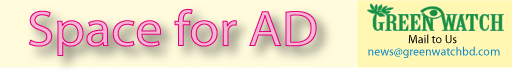- Inqilab Monch Seeks Home Adviser’s Exit |
- UN Calls for Calm in Bangladesh After Protest Leader’s Killing |
- DMP issues 7 traffic directives for Osman Hadi’s Janaza |
- Vested quarter fuelling chaos to impose new fascism: Fakhrul |
- Hadi’s namaz-e-janaza at 2:30pm Saturday |
মঙ্গোলদের হাতে ধ্বংস হওয়ার আগে কেমন ছিল বাগদাদের বিখ্যাত লাইব্রেরি?

ঘটনাটি ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি একটি সময়ের। মঙ্গোল সৈন্যবাহিনীর টানা অবরোধের মুখে আত্মসমর্পণ করেন আব্বাসীয় বংশের শাসক আল মুস্তাসিম।
এরপরের ইতিহাসটা হয়তো অনেকেরই জানা।
ইতিহাসবিদদের মতে, দখল নেওয়ার পর মঙ্গোল সেনাপতি হুলেগু খান, যিনি হালাকু খান নামেও পরিচিত, তার নেতৃত্বে মঙ্গোল সেনারা আব্বাসীয় খিলাফতের রাজধানী বাগদাদে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।
হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়, ধ্বংস করে ফেলা হয় গুরুত্বপূর্ণ অসংখ্য স্থাপনা।
ধ্বংসপ্রাপ্ত সেইসব স্থাপনার মধ্যে ‘বাইত আল-হিকমাহ’ নামের একটি লাইব্রেরিও ছিল, যাকে ইসলামের স্বর্ণযুগের অন্যতম বড় নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।
এটি এতটাই সমৃদ্ধ ছিল যে, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সারা বিশ্বের পণ্ডিতরা সেসময় জ্ঞান চর্চার জন্য বাগদাদে উপস্থিত হতেন।
ফলে শহরটি দ্রুতই জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছিল বলে জানা যায়।
প্রাচীন সেই গ্রন্থাগারটির কোনো অবকাঠামোই এখন আর টিকে নেই।
১২৫৮ সালের শুরুর দিকে বাগদাদ দখলের পর মঙ্গোলরা লাইব্রেরিটি পুরোপুরি ধ্বংস করে ফেলে।
গবেষকদের মতে, গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত বইগুলোর বড় একটি অংশই তখন পুড়িয়ে ছাই করা হয়। বাকিগুলো ফেলে দেওয়া হয় শহরের পাশ দিয়ে বয়ে চলা টাইগ্রিস বা দজলা নদীতে।
লোকমুখে গল্প প্রচলিত আছে যে, পুড়িয়ে ফেলার পরও এত বিশাল সংখ্যক বইয়ের পাণ্ডুলিপি তখন টাইগ্রিসে ছুড়ে ফেলা হয়েছিল যে, সেগুলোর কালি মিশে নদীটির পানির রঙ কালো হয়ে গিয়েছিল।
যদিও বাস্তবে এমন কিছু আদৌ ঘটেছিল কি না, সেটি নিয়ে বিতর্ক আছে।
তবে গ্রন্থাগারটি যে তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম বড় জ্ঞানকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল, সে বিষয়ে অধিকাংশ গবেষকই একমত হয়েছেন।
কিন্তু ধ্বংস হওয়ার আগে লাইব্রেরিটি দেখতে কেমন ছিল? সেখানে কী ধরনের বই পাওয়া যেত এবং সেগুলো সংগ্রহই-বা করা হয়েছিল কীভাবে?
কে প্রতিষ্ঠা করেছিল?
আরবি ‘বাইত আল-হিকমাহ’ শব্দের বাংলা অর্থ করলে দাঁড়ায় ‘জ্ঞানগৃহ’।
পশ্চিমা ইতিহাসবিদ এবং গবেষকরা একে ‘হাউজ অব উইজডম’ নামেও ডেকে থাকেন।
প্রসিদ্ধ এই লাইব্রেরিটিকে ইসলামের স্বর্ণযুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যেটি গড়ে উঠেছিল আব্বাসীয় বংশের শাসনামলে।
ইতিহাসবিদদের মতে, শুরুর দিকে এটি ছিল আব্বাসীয় শাসকদের ব্যক্তিগত পাঠাগার, যা পরবর্তীতে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।
তবে শাসকদের মধ্যে ঠিক কে এই লাইব্রেরিটি গড়ে তুলেছিলেন, সেটি নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে তিন ধরনের মত প্রচলিত রয়েছে বলে একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন ইউনিভার্সিটি ইসলাম মালয়েশিয়ার শিক্ষক ড. আদেল আবদুল আজিজ।
‘ইসলামি গ্রন্থাগারগুলোর উপর বাইত আল হিকমাহর প্রভাব’ শীর্ষক ওই প্রবন্ধে অধ্যাপক আজিজ বলছেন, আব্বাসীয় বংশের দ্বিতীয় শাসক আবু জাফর আল মনসুরের সময়েই প্রথম ‘বাইত আল হিকমাহ’ প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয় বলে গবেষকদের অনেকে উল্লেখ করেছেন।
তাদের মতে, ব্যক্তিগত আগ্রহের জায়গা থেকেই ওষুধ, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, প্রকৌশল, ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্যসহ নানান বিষয়ের উপর বই সংগ্রহ শুরু করেন খলিফা আল মনসুর।
“তিনি বিজ্ঞান পড়ার বিষয়ে মুসলমানদের উৎসাহ দেওয়ার পাশাপাশি নিজেদের মেধার বিকাশ সাধনে অনুপ্রাণিত করেছিলেন,” ইরাকি গবেষক এস আল দিয়াজির বরাত দিয়ে লিখেছেন অধ্যাপক আজিজ।
খলিফা আল মনসুরের শাসনামলে গ্রিক, ফার্সি, সংস্কৃতসহ আরও বেশ কয়েকটি ভাষার গুরুত্বপূর্ণ বই আরবিতে অনুবাদ করা শুরু হয়েছিল বলেও দাবি করেন গবেষকদের কেউ কেউ।
আর এভাবেই আব্বাসীয় দ্বিতীয় খলিফার সময় ‘বাইত আল-হিকমাহ’র ভিত্তি রচিত হয়েছিল বলে দাবি করেন তারা।
তবে ইতিহাসবিদদের দ্বিতীয় দলটি অবশ্য এই মতকে সমর্থন করছেন না।
তারা বলছেন, বাগদাদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারটি গড়ে উঠেছিল আরও পরে, বিখ্যাত খলিফা হারুন আল রশিদের সময়ে।
“খলিফা হারুন আল রশিদের শাসনামলে বুদ্ধিবৃত্তিক জায়গায় বেশ উন্নতি হয়েছিল, বিশেষত অনুবাদ আন্দোলনের সময়,” বলছেন ইউনিভার্সিটি ইসলাম মালয়েশিয়ার শিক্ষক অধ্যাপক আজিজ।
আরব, ইরান এবং সিরিয়া অঞ্চলের বহু পণ্ডিতকে একত্রিত করে আব্বাসীয় বংশের পঞ্চম খলিফা আল রশিদ অন্য ভাষার বহু বই আরবিতে অনুবাদ করিয়েছিলেন বলেও জানা যায়।
‘বাইত আল-হিকমাহ’ যে খলিফা হারুন আল রশিদের শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেটির প্রমাণ হিসেবে গবেষকদের অনেকেই দ্বাদশ শতকের বিখ্যাত মুসলিম ইতিহাসবিদ ইয়াকুত ইবনে আব্দুল্লাহর একটি লেখার বরাত দিয়ে থাকেন।
ইয়াকুত ইবনে আব্দুল্লাহ তার একটি গ্রন্থে আবু নবম শতকের মুসলিম পণ্ডিত ঈসা আল ওয়াররাকের উল্লেখ করে বলেছেন যে, তিনি খলিফা আর রশিদ এবং আল মামুনের সময় ‘বাইত আল হিকমাহ’র জন্য বিভিন্ন বইয়ের অনুলিপি তৈরি করতেন।
কিন্তু এমন প্রমাণ হাজির করার পরও গবেষকদের মধ্যে তৃতীয় একটি দল রয়েছেন যারা মনে করেন, পূর্বসূরিদের সংগ্রহ করা বই নিয়ে খলিফা হারুন আল রশিদের পুত্র আল মামুনই আসলে বাগদাদের লাইব্রেরিটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ ডি লেসি ইভানস ও’লিয়ারিও এই মতকে সমর্থন করেছেন।
মি. ও’লিয়ারি বলছেন, “খলিফা আল মামুন একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন, যেটির নাম তিনি দিয়েছেন ‘বাইত আল হিকমাহ’। সেখানে গ্রিক ভাষার বইগুলোর অনুবাদ করা হয়।”
মার্কিন ইতিহাসবিদ উইলিয়াম জেমস ডুরান্টসহ আরও অনেকের লেখাতেও প্রায় একই ধরনের মতামত পাওয়া গেছে বলে জানাচ্ছেন ইউনিভার্সিটি ইসলাম মালয়েশিয়ার শিক্ষক আদেল আবদুল আজিজ।
“কাজেই এ কথা বলা যায় যে, আল মামুনের অনেক আগে থেকেই বাগদাদে ‘বাইত আল হিকমাহ’র অস্তিত্ব ছিল। তবে সম্ভবত তার শাসনামলেই গ্রন্থাগারটি আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল,” বলেন অধ্যাপক আজিজ।
নবম শতকের বিভিন্ন দলিলপত্র থেকে গবেষকরা জানতে পেরেছেন যে, আব্বাসীয় বংশের সপ্তম শাসক আল মামুন ইবনে হারুনের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি বেশ আগ্রহ ছিল।
ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি এগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা বাড়িয়ে দেন, যার ফলে ‘বাইত আল হিকমাহ’র সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।
গ্রন্থাগারটি ছিল কোথায়?
তৎকালীন লেখক ও ইতিহাসবিদদের একাধিক লেখায় ‘বাইত আল হিকমাহ’র উল্লেখ পাওয়া গেলেও সেটির অবস্থান নিয়ে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না।
তবে শুরুর দিকে যেহেতু এটি আব্বাসীয় খলিফাদের ব্যক্তিগত লাইব্রেরি ছিল, সেখান থেকেই ধারণা করা হয় যে, প্রথমদিকে এর অবস্থান ছিল রাজপ্রাসাদের ভেতরেই কোনও একটি জায়গায়।
খলিফা হারুন আল রশিদের সময়েও পাঠাগারটি রাজপ্রাসাদের সঙ্গে ছিল বলে ধারণা ইতিহাসবিদদের।
তবে কেউ কেউ ভিন্ন মত পোষণ করে বলেছেন যে, ঠিক ভেতরে নয়, বরং রাজপ্রাসাদের গা ঘেঁষে গড়ে তোলা একটি বড় ঘরে বইগুলো রাখা হতো।
কিন্তু পরবর্তীকালে খলিফা আল মামুনের সময় যখন বইয়ের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে, তখন স্থানান্তর করে লাইব্রেরিটি বাগদাদের পূর্ব অংশে টাইগ্রিস নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে সরিয়ে নেওয়া হয় বলে জানাচ্ছেন গবেষকরা।
ইরাকের স্থানীয় কয়েক জন গবেষকের বরাত দিয়ে অধ্যাপক আজিজ লিখেছেন যে, গ্রন্থাগারটি সরিয়ে আল রুসাফা নামক একটি স্থানে নেওয়া হয়, যেটি টাইগ্রিস নদীর পূর্বপাশে অবস্থিত ছিল।
যদিও লাইব্রেরিটি আদৌ সরিয়ে দূরে নেওয়া হয়েছিল কি না, সেটি নিয়েও মতভেদ রয়েছে।
গবেষকদের কেউ কেউ মনে করেন যে, বইয়ের সংখ্যা বেড়ে বৃদ্ধি পাওয়ার পর তৈরি করা নতুন ভবনটি রাজপ্রাসাদের কাছেই কোনও একটি জায়গায় নির্মাণ করা হয়ে থাকতে পারে।
“হাউজ অব উইজডম ঠিক কোথায় বা কবে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেটির পূঙ্খানুপূঙ্খ বিশ্লেষণ আসলে আমাদের জন্য খুব বেশি জরুরি নয়,” বিবিসি ফিউচারকে বলেন যুক্তরাজ্যের সারে বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক জিম আল খলিলি।
তিনি আরও বলেন, “জরুরি হলো এসব বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলোর ইতিহাস এবং সেগুলো কীভাবে আজ এ পর্যায়ে আসলো।”
দেখতে কেমন ছিল লাইব্রেরিটি?
গবেষকদের বরাত দিয়ে অধ্যাপক আজিজ বলছেন, নতুন লাইব্রেরি ভবনটি ছিল পরিকল্পিত এবং বেশ নান্দনিক।
“খলিফা আল মনসুরের সময় নির্মিত ‘গোল্ডেন ক্যাসল’ নিয়ে গবেষণাকালে ‘বাইত আল হিকমায়’ একটি চমৎকার স্থাপত্য পরিকল্পনা খুঁজে পেয়েছেন গবেষক মাহমুদ আহমাদ ডারবিশ,” বলেন অধ্যাপক আজিজ।
সেখান থেকে জানা যায়, নতুন লাইব্রেরি ভবনে বই রাখার জায়গার পাশাপাশি মহাকাশ নিয়ে গবেষণার জন্য একটি মানমন্দিরও তৈরি করা হয়েছিল।
গবেষকদের মতে, গ্রন্থাগারটির ভেতরে একটি বড় খোলা জায়গা ছিল। চারদিক দিয়ে সেটি দুই তলাবিশিষ্ট বেশ কয়েকটি বড় কক্ষ দিয়ে ঘেরা ছিল।
ভবনের চারকোণে ছিল বড় বড় চারটি গম্বুজ। এছাড়া পাঠাগারের প্রধান ঘরটির উপরেও বিশাল আকারের একটি উঁচু গম্বুজ ছিল।
ভবনের নিচের তলায় দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো সারি সারি আলমারিতে বই রাখা হতো।
এক্ষেত্রে ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্যসহ প্রতিটি বিষয়ের বইয়ের জন্য আলাদা তাক ছিল, যাতে সহজেই সেগুলো খুঁজে পাওয়া যায়।
লাইব্রেরিতে পড়াশোনার ব্যবস্থার পাশাপাশি ছিল অনুবাদ, অনুলিপি, বাঁধাই এবং লেখার জন্য আলাদা জায়গা ছিল।
এসব কাজের জন্য দক্ষ লোক নিয়োগ দেওয়া হতো, যারা বেশ ভালো বেতন পেতেন।
মুসলমানদের পাশাপাশি অন্য ধর্মের পণ্ডিতদেরও সেখানে কাজ করতে পারতেন বলে জানাচ্ছেন গবেষকরা।
লেখক, অনুবাদক, ছাত্র এবং কর্মচারীদের জন্য ভবনের উপরের তলায় থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা রাখা হয়েছিল।
নদীর কাছাকাছি অবস্থিত হওয়ায় লাইব্রেরির চারপাশের পরিবেশও বেশ চমৎকার ও মনোরম ছিল বলে জানাচ্ছেন গবেষকরা।
কী কী ধরনের বই ছিল?
গবেষকরা বলছেন যে, তৎকালীন সময়ে লিখিত জ্ঞানগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রায় সব বই-ই পাওয়া যেত ‘বাইত আল হিকমা’তে।
এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল চিকিৎসা, বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস এবং সাহিত্যের বই।
বইয়ের সংখ্যার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনও তথ্য না পাওয়া গেলেও লাইব্রেরিটিতে কয়েক লাখ বই, পাণ্ডুলিপি এবং দলিলপত্র ছিল বলে ধারণা করেন ইতিহাসবিদরা। যদিও বইয়ের এই 'লাখ' সংখ্যা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে।
অনেকে মনে করেন, গ্রন্থাগারটতে বইয়ের তুলনায় রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন দলিলপত্রের সংখ্যাই বেশি ছিল।
তবে বিবিসি ফিউচার তাদের একটি প্রতিবেদনে বলছে যে, বর্তমানে লন্ডনের বৃটিশ লাইব্রেরি বা প্যারিসের বিবলিওতেক ন্যাসিওনালে যে পরিমাণ বইয়ের সংগ্রহ, অতীতে হাউজ অব উইজডমেও তেমনটি ছিল।
মঙ্গোলদের আক্রমণের আগে সেসব গ্রন্থের মধ্যে অল্পকিছু সরানো সম্ভব হয়েছিল।
এক্ষেত্রে গবেষকদের অনেকেই পারস্যের মুসলিম পণ্ডিত নাসিরুদিন আল তুসির নাম উল্লেখ করেন, যিনি অল্প কিছু বইয়ের পাণ্ডুলিপি রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে জানা যায়।
বাগদাদের বড় লাইব্রেরিতে আরবি ভাষার অনেক মৌলিক বই ছিল।
তবে মোট সংগৃহীত বইয়ের বেশিরভাগই ছিল অন্য ভাষা থেকে আরবিতে অনুবাদ করা।
দশম শতকের লেখক ও ইতিহাসবিদ ইবনে আল নাদিম তার ‘আল ফিরিস্ত’ নামক গ্রন্থে অন্তত ৬৭ জন অনুবাদকের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা বাইত আল হিকমাহ’র জন্য কাজ করতেন।
এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রায় ৪৭ জনই কাজ করতেন গ্রিক ও সিরীয় ভাষার গ্রন্থ অনুবাদে।
সেসময়ের উল্লেখযোগ্য অনুবাদকদের মধ্যে আবু মাশার, হুনাইন ইবনে ইসহাক, ইবনুল আসসাম ও সাবিত ইবন কুররা, হাজ্জাজ ইবনে মাতির, আল কিন্দি, আল বুলবাকিসহ আরও অনেকের নাম পাওয়া যায়।
এর মধ্যে গ্রিক ভাষায় লেখা বই অনুবাদ করে আল কিন্দি এবং হুনাইন ইবনে ইসহাক বেশ নাম করেছিলেন বলে জানা যায়।
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক বই অনুবাদ করা হয়েছিল। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি বই হচ্ছে, গ্রিক চিকিৎসক পেডানিয়াস ডায়োস্কোরাইডসের ‘ম্যাটেরিয়া মেডিকা’।
চিকিৎসা বিজ্ঞানের বাইরে, গণিত, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ঔষধ, রসায়ন, এবং প্রকৌশল বিদ্যার বইও লাইব্রেরির সংগ্রহে ছিল।
আরও ছিল ধর্ম ও দর্শনের বই। এক্ষেত্রে কোরান-হাদিস ছাড়াও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বই সংগ্রহে রাখা হতো। পাশাপাশি অন্য ধর্মের ভাবনাও লাইব্রেরিতে স্থান পেয়েছিল বলে জানা যায়।
এখনকার মতো তখনও সাধারণ মানুষজন লাইব্রেরিতে গিয়ে বই পড়তে পারতেন, এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে তাদেরকে বই ধারও দেওয়া হতো।
অনুবাদ বই ছাড়াও লাইব্রেরিতে গুরুত্বপূর্ণ অনেক মৌলিক বইয়ের পাণ্ডুলিপি, স্থাপত্যের নকশা, মানচিত্র, দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি রাখা হতো বলে জানাচ্ছেন ইতিহাসবিদরা।
কীভাবে এত বই সংগ্রহ হয়েছিল?
বাগদাদের বড় লাইব্রেরিটি সমৃদ্ধ করার পেছনে অনুবাদ আন্দোলনের ভূমিকা বড় করে দেখে থাকেন ইতিহাসবিদরা।
মূলত অষ্টম শতকে বাগদাদে এই বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল, যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আব্বাসীয় খলিফারা নিজেই।
এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ও মতের সঙ্গে পরিচয় ঘটানোর মাধ্যমে মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাধারাকে সমৃদ্ধ করা।
এই আন্দোলনের ফলে তখন ফার্সি, গ্রিক, ল্যাটিন, সিরীয়, মিশরীয়, চীনা, সংস্কৃতসহ অন্যান্য ভাষায় রচিত অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ বই আরবিতে অনুবাদ করা সম্ভব হয়েছিল বলে জানান গবেষকরা।
প্রায় দেড়শ বছর ধরে চলা অনুবাদ আন্দোলনের শুরুটা হয়েছিল ফার্সি ভাষার গুরুত্বপূর্ণ কিছু বই অনুবাদের মাধ্যমে।
আব্বাসীয় শাসকরা আরবি ভাষায় লিখিত বই সংগ্রহ করার পাশাপাশি ফার্সির বইগুলো মাতৃভাষায় রূপান্তরের উদ্যোগ নেন।
এরপর ধীরে ধীরে অন্য ভাষার বইগুলোও আস্তে আস্তে অনুবাদ হতে থাকে।
এক্ষেত্রে অন্য ভাষার মূল বই কেনা, অনুলিপি তৈরি করা, এমনকি ধার করে এনেও অনেক সময় অনুবাদ করা হতো।
“আব্বাসীয় শাসকরা বই কেনার জন্য চুক্তি করেছিলেন এবং এর জন্য উচ্চমূল্যও প্রদান করেছিলেন, বিশেষত খলিফা আল মামুনের সময়ে,” বলেন গবেষক ড. হাসান আহমদ মাহমুদ।
যুদ্ধজয়ের মাধ্যমেও কিছু বই সংগৃহীত হয়ে থাকতে পারে বলেও ধারণা করেন ইতিহাসবিদরা।
অনুবাদ করার পর সেটিও কয়েকটি অনুলিপি তৈরি করা হতো, যাতে একটি নষ্ট হয়ে গেলেও অন্যটি সংরক্ষণ করা যায়।
নবম শতকে খলিফা আল মামুনের সময় আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ হয়।
বাইত আল হিকমাহতে গ্রিক ভাষা থেকে অনুবাদ করা বইয়ের সংখ্যা ছিল চোখে পড়ার মতো।
তখন যাদের কাছে গ্রিকভাষার বই ছিল, চিঠি পাঠিয়ে তাদের কাছ থেকে বই ধার করে আনার নজিরও পাওয়া গেছে বলে জানাচ্ছেন গবেষকরা।
এর একটি কারণ হিসেবে তারা বলছেন, জ্ঞানচর্চার এক পর্যায়ে আরবরা গ্রিক মনীষীদের দর্শন, সাহিত্য এবং চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞানের প্রতি বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন।
ফলে গ্রিক ভাষার বই আরবিতে অনুবাদের জন্য ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে উচ্চ বেতনে পণ্ডিত নিয়োগ দেন আব্বাসীয় শাসকরা।
মূলত সেই কারণেই কয়েক দশকের মধ্যে প্লেটো, অ্যারিস্টটল, হিপোক্রেটিস, টলেমি, পিথাগোরাস, আর্কিমিডিস, গ্যালেন, ইউক্লিড-সহ অসংখ্য মনীষীর লেখা গ্রিক ভাষার আকরগ্রন্থগুলো তখন আবরিতে অনুবাদ করা সম্ভব হয়েছিল বলে মনে করেন ইতিহাসবিদরা।
‘বইয়ের ওজনে স্বর্ণ’
কথিত আছে যে, অন্য ভাষার গুরুত্বপূর্ণ কোনও জ্ঞানগ্রন্থ আরবিতে অনুবাদ করলে সেই গ্রন্থের ওজনের সমপরিমাণ স্বর্ণ উপহার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন আব্বাসীয় বংশের শাসকরা।
ইউনিভার্সিটি ইসলাম মালয়েশিয়ার শিক্ষক অধ্যাপক ড. আদেল আবদুল আজিজ বলছেন,“গ্রিক ভাষার প্রাচীন গ্রন্থগুলো অনুবাদের জন্য খলিফা আল মামুন তৎকালীন বিখ্যাত অনুবাদক হুনাইন ইবনে ইসহাককে বইয়ের ওজনে স্বর্ণ প্রদানের এমন প্রস্তাব দিয়েছিলেন বলে একাধিক সূত্রে উল্লেখও করা হয়েছে।”
যদিও এর পক্ষে শক্ত কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে জানাচ্ছেন পশ্চিমা গবেষকরা।
তবে লেখক, গবেষক এবং অনুবাদদেরকে যে তাদের কাজের জন্য সেসময় মোটা অঙ্কের বেতন দেওয়া হতো, সে বিষয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায় না।
মার্কিন ইতিহাসবিদ উইলিয়াম জেমস ডুরান্টের লেখা থেকে জানা যায় যে, খলিফা আল মামুনের সময়ে ‘বাইত আল হিকমাহ’র ব্যয় স্বর্ণ-রোপ্য মিলে প্রায় দুই লক্ষ মুদ্রায় পৌঁছেছিল।
শাসকদের পাশাপাশি বিদ্যানুরাগী ধনী ব্যক্তিরাও লাইব্রেরির তহবিলে অর্থ দান করতেন বলে জানাচ্ছেন গবেষকরা।
বিবিসি ফিউচারের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, ‘হাউজ অব উইজডমে’র কারণে তৎকালীন বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে পণ্ডিত, গবেষক এবং বিজ্ঞানীরা বাগদাদে হাজির হতে শুরু করেন।
ফলে ক্রমেই লাইব্রেরিটি জ্ঞান চর্চার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে এবং বিভিন্ন ধরনের বই পড়ার ক্ষেত্রে সেটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী এক কেন্দ্রে পরিণত হয়।
একই সঙ্গে সেটি প্রকাশের স্বাধীনতারও প্রতীক হয়ে উঠে। এর কারণ সেখানে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিদ্বানরা ঢুকতে পারতেন এবং পড়াশোনা-গবেষণার অনুমতিও পেতেন।
নবম শতকের পর লাইব্রেরিটি ক্রমেই একটি একাডেমিতে পরিণত হয়।
‘বাইত আল হিকমাহ’তে তখন মানবিক ও বিজ্ঞান, গণিত, চিকিৎসা, রসায়ন, ভূগোল, দর্শন, সাহিত্য ও শিল্পকলা, এমনকি আলকেমি ও জ্যোতিষশাস্ত্রের মতো বিষয়েরও চর্চা হতে থাকে।
ফলে বুদ্ধিবৃত্তিক জায়গা থেকে তখন মুসলিম বিশ্ব তাদের সবচেয়ে উজ্জ্বলতম সময়ে পৌঁছায়, যা 'ইসলামের স্বর্ণযুগ’ নামে পরিচিত।
বিখ্যাত গণিতবিদ আল খারিজমি এই সময়েই ‘কিতাবুল জাবর’ লিখেছিলেন, যা পরবর্তীতে গণিতশাস্ত্রকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে ইতালীয় পণ্ডিত ফিবোনাচ্চি-সহ পশ্চিমের অসংখ্য মনীষীকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে বলে জানা যায়।
গণিতে অসাধারণ অবদানের জন্য আল খারিজমিকে প্রায়শই “বীজগণিতের জনক” ডাকা হয়ে থাকে।
মুসলিম দার্শনিক আল জাহিজের নামও বেশ জোরে উচ্চারিত হয়, যিনি ব্রিটিশ বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনেরও প্রায় এক হাজার বছর আগে প্রাণিদের বিবর্তনের উপর ‘কিতাব আল-হায়ওয়ান’ নামে একটি বই লিখেছিলেন।
এছাড়া চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, প্রকৌশলবিজ্ঞানসহ জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অবদান রাখার জন্য হুনাইন ইবনে ইসহাক, আল কিন্দি, আল-মালিক, বনু মুসা, মুহাম্মদ জাফর ইবনে মুসা, ইবনে আলি, আল জাজারি প্রমুখ মনীষীর নাম স্মরণ করা হয়।
জ্ঞানের জগতে তাদের অবদানের পেছনে 'বাইত আল হিকমাহ'র ভূমিকা রয়েছে। তবে সেই ভূমিকা কতটুকু, সেটি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।